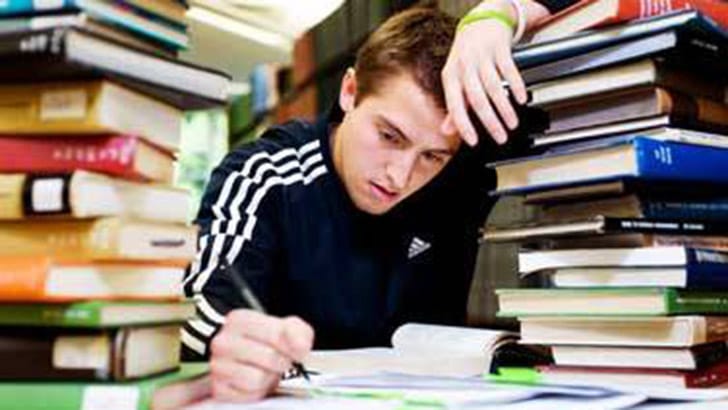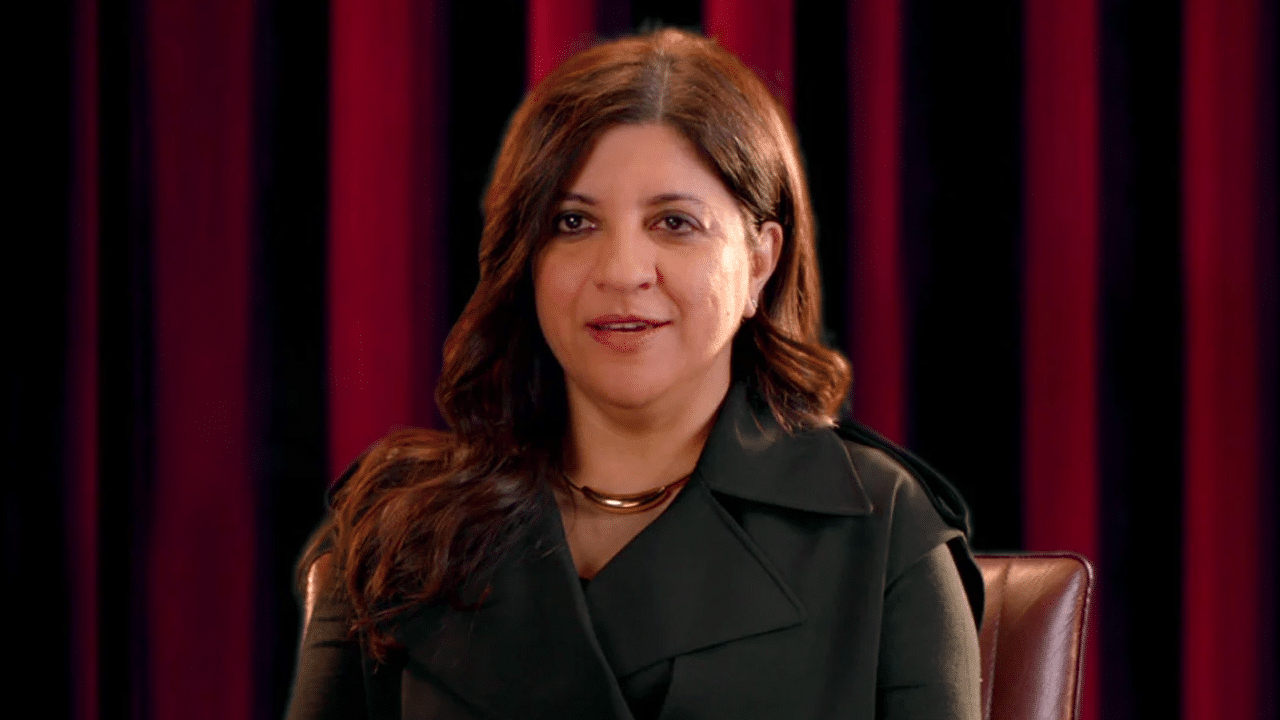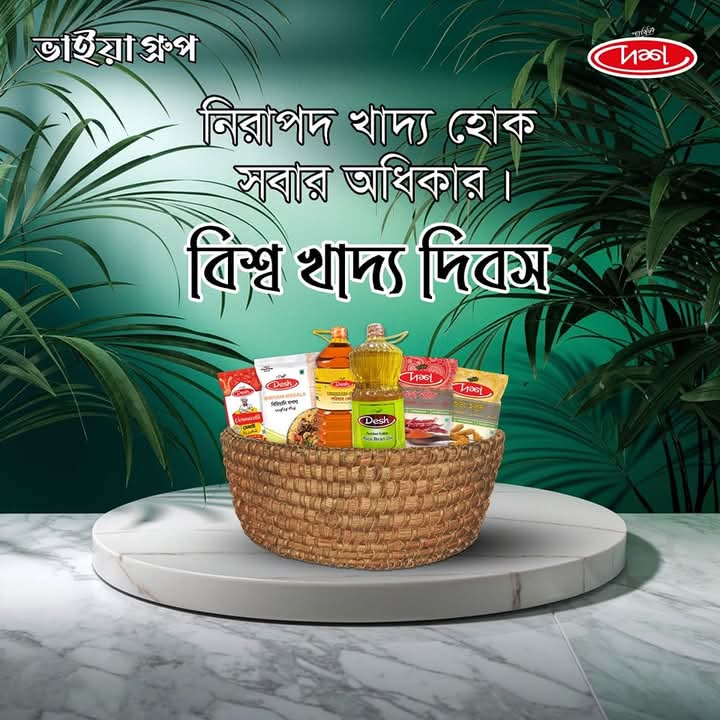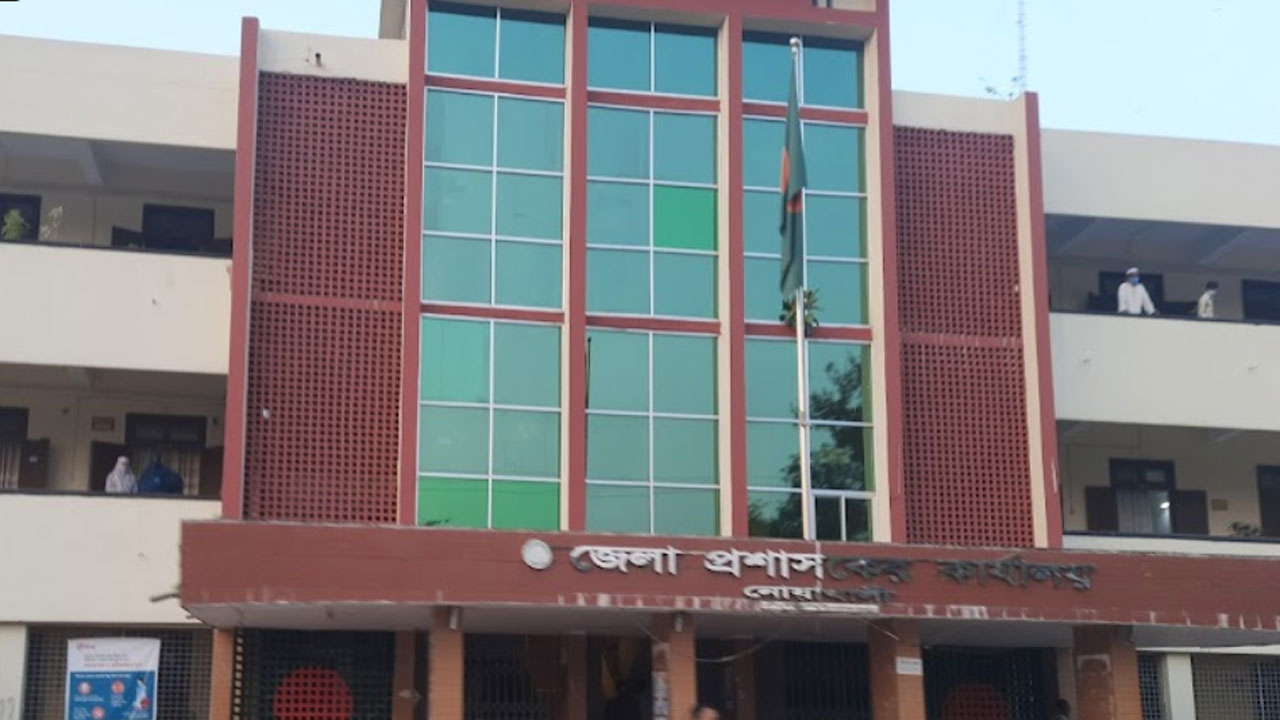জুবাইয়া বিন্তে কবির:
আজকের দিনে শিক্ষার আসল অর্থ যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা কেবল জানার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, শেখার আনন্দ যেন কোথাও হারিয়ে ফেলেছি। এখন একজন শিক্ষার্থী কী শিখছে, তার চিন্তাশক্তি কতটা প্রসারিত হচ্ছে—এসব প্রশ্ন যেন আর কারও মাথায় আসে না। মা-বাবারা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অস্থির; একের পর এক প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেন্টার, মডেল টেস্ট—সব আয়োজন সম্পন্ন, কিন্তু সেই শিশুটির চোখে কি সত্যিই জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠছে? সে কি মানুষ হয়ে উঠছে? নাকি আমরা কেবল তাকে একটি নম্বরের পেছনে ছুটতে শেখাচ্ছি?
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে মন ভরে ওঠে গভীর বেদনায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ মুখস্থবিদ্যার শিকলে আবদ্ধ। অথচ শিক্ষা তো কেবল তথ্য আহরণের নাম নয়—এ এক আত্মজাগরণের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে গড়ে ওঠে মনন, বিবেক, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা। কিন্তু আজ সেই আলোর পথ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। আমাদের সন্তানরা এখন প্রতিযোগিতার এক যান্ত্রিক দৌড়ে অংশ নিচ্ছে, যেখানে ‘জিপিএ’ নামের একটি সংখ্যা হয়ে উঠেছে সফলতার মাপকাঠি—আর মানুষ হয়ে ওঠার আনন্দ, ভাবনা ও স্বপ্ন হারিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। শিক্ষার এই সংকট শুধু পাঠ্যবইয়ের নয়, এটি এক গভীর মানবিক সংকট। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগুক—আমরা কি আমাদের সন্তানদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছি, নাকি নিঃসাড় যন্ত্রে রূপ দিচ্ছি?

অন্যদিকে, স্কুল-কলেজের ব্যবস্থাপনাও আজ জিপিএ দৌড়ে মেতে উঠেছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যত বেশি ‘গোল্ডেন জিপিএ’ উৎপাদন করতে পারবে, ততই তার গৌরব। সংবাদপত্রে রঙিন ছবিতে সেই শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, ব্যানার-ফেস্টুনে ঝুলে থাকে অভিনন্দনের বন্যা। অথচ সেই সংবর্ধনা আসলে মুখস্থবিদ্যার জয়োৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যেন ভুলে গেছি, জ্ঞান অর্জন মানে শুধু বইয়ের পাতা মুখস্থ করা নয়—জ্ঞান মানে ভাবতে শেখা, বিশ্লেষণ করা, মানবিক হওয়া। এ প্রসঙ্গে নলছিটি সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অধ্যাপিকা মাহমুদা বেগম পাখি এক গভীর সত্য উচ্চারণ করেন, “আমাদের শিক্ষা এখন আর আত্মার আহার নয়, পরীক্ষার পণ্য হয়ে গেছে। শিশুরা শিখছে উত্তর লিখতে, প্রশ্ন করতে নয়। অথচ প্রশ্ন করার সাহসই জ্ঞানার্জনের প্রথম শর্ত। আমরা যদি তাদের মুখস্থের খাঁচা থেকে বের করতে না পারি, তবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে কেবল ডিগ্রিধারী রোবটের দেশ, মানুষ নয়।” তার এই কথাগুলো আমাদের আত্মসমালোচনায় বাধ্য করে। সত্যিই তো, আজ আমরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলছি যারা জানে ‘কীভাবে পাস করতে হয়’, কিন্তু জানে না ‘কেন শিখতে হয়’।
বহুধারার শিক্ষার বিভাজন: এক রাষ্ট্রে তিন জাতি : আরও এক ভয়ংকর বাস্তবতা হলো—আমাদের দেশে বিদ্যমান বহুধারার শিক্ষা ব্যবস্থা। সাধারণ শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা, এবং মাদ্রাসা শিক্ষা—এই তিনটি ধারায় বিভক্ত আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। সাধারণ ধারার শিক্ষার্থীরা মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, কিন্তু সীমিত সুযোগ ও প্রতিযোগিতার চাপে তাদের শেখার আনন্দ হারিয়ে যায়।

অন্যদিকে, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা—যাদের বড় অংশ আসে বিত্তবান পরিবার থেকে—দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের চেয়ে বিদেশমুখী জীবনেই বেশি আগ্রহী। অনেকের কাছে বাংলাদেশ কেবল একটি ‘স্টেপিং স্টোন’, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা বিদেশে পাড়ি জমায়। আর মাদ্রাসা শিক্ষায় রয়েছে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা—যাদের অনেকেই আধুনিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির আলো থেকে বঞ্চিত। সেখানে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, যা সমাজের মূলধারার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র দুর্বল করে দেয়। ফলে আমরা একই দেশে তিন ভিন্ন মানসিকতার নাগরিক তৈরি করছি—যার প্রত্যেকে অন্যের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, “রাষ্ট্র একটি একমুখী, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।” সেই স্বপ্ন আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে।
মানুষ তৈরি না হয়ে তৈরি হচ্ছে যন্ত্র : এক সময় আমরা গর্ব করে বলতাম—“শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো মানুষ তৈরির কারখানা।” কিন্তু এখন সেই কারখানায় তৈরি হচ্ছে শুধু পরীক্ষামুখী, আত্মকেন্দ্রিক, সুবিধাবাদী মানুষ। যাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বার্থ, পদোন্নতি, ধনসম্পদ।
মানুষ আমরা তাকেই বলি, যার মধ্যে আছে মানবিকতা, সহমর্মিতা, নীতি, দায়িত্ববোধ। একজন সুশিক্ষিত মানুষ কখনও তার জ্ঞানকে অন্যায়-অনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু আজ যারা দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে, তারা অনেকেই ক্ষমতা ও অর্থের মোহে নীতিহীনতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এত ডিগ্রি, এত সনদ—কিন্তু কোথায় সেই আলো, যা মানুষের হৃদয় আলোকিত করবে?
সৃজনশীল শিক্ষার পথে: আনন্দ ও শিল্পের সংযোগ : শিক্ষা শুধু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়েরও বিকাশ ঘটায়। তাই মুখস্থবিদ্যার শিকল ভেঙে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে ‘শিক্ষাসহায়ক কার্যাবলি’ বা co-curricular activities হতে পারে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। আমাদের শিক্ষানীতিতে এর জন্য আলাদা অনুদানও নির্ধারিত আছে—কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে তা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। অথচ নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, নাটক, সাহিত্য ও বিতর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে আনন্দ ও মুক্তচিন্তার সঞ্চার ঘটায়, তা বইয়ের পাতায় পাওয়া যায় না। চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিশুর মন মুক্ত হয়; রঙের স্পর্শে সে আবিষ্কার করে পৃথিবীর সৌন্দর্য। গান তাকে শেখায় সুরের শৃঙ্খলা, নাচ শেখায় তাল-লয়ের সাদৃশ্য। এইসব শিল্পচর্চা শিশুদের একঘেয়েমি দূর করে, তাদের মনোযোগ, দলবদ্ধতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিতভাবে এই কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করত, তাহলে শিশুদের মধ্যে শেখার প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠত। তারা শিক্ষা পেত কেবল পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্য। অধ্যাপিকা মাহমুদা বেগম পাখি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, “একটি শিশুর হাতে যখন তুলির আঁচড়, তার মনে তখন জেগে ওঠে পৃথিবীর রঙ। যখন সে গান শেখে, তখন তার ভিতর গড়ে ওঠে শৃঙ্খলা, সংবেদনশীলতা আর আনন্দের বোধ। এই বোধটাই পরবর্তীতে তাকে মানুষ হতে শেখায়। শিক্ষা যদি আনন্দ না দেয়, তবে তা আত্মার বিকাশ ঘটাতে পারে না।” তার এই ভাবনাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সত্যিকারের শিক্ষা কখনো বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; তা হৃদয়ে বিকশিত হয়।

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ: মানবসম্পদের পূর্বশর্ত : কোনো দেশ যদি সত্যিই উন্নত হতে চায়, তবে তাকে শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে—এ কথা বারবার ইতিহাসে প্রমাণিত। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী, সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের জিডিপির অন্তত ৬% শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই হার এখনো ২% এর আশপাশে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দুর্বল, শিক্ষক সংকট প্রকট, আর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা হতাশাজনক। এই বাস্তবতায় আমরা কিভাবে মানসম্মত শিক্ষা প্রত্যাশা করব? যদি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে শহর-গ্রামের বৈষম্য কমবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীরা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাবে, শিক্ষকরা নিশ্চিন্ত মনে পড়াতে পারবেন। শিক্ষার পরিবেশে ফিরবে প্রাণ।
এই প্রসঙ্গে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, “শিক্ষায় বিনিয়োগ মানে ভবিষ্যতে বিনিয়োগ। উন্নত মানবসম্পদ ছাড়া কোনো দেশ এগোতে পারে না। শিক্ষার মূলধন শুধু বই বা ভবন নয়—এটি মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ। শিক্ষককে মর্যাদা না দিলে, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার না দিলে, জাতি কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।” তার এই বক্তব্য আমাদের পথ দেখায়। সত্যিই, শিক্ষায় ব্যয়ের প্রতিটি টাকাই ভবিষ্যতের বীজ। যদি সে বীজ যথাযথ যত্নে রোপণ করা যায়, তবে বাংলাদেশ একদিন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে।
যুগোপযোগী শিক্ষানীতি: পরিবর্তনের চাবিকাঠি : সবশেষে প্রয়োজন একটি সময়োপযোগী, সর্বজনীন, এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি—যেখানে মুখস্থ বিদ্যার স্থান থাকবে না। সেই নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য, নৈতিক শিক্ষা, প্রযুক্তি দক্ষতা, শিল্প ও ক্রীড়া।
এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চাই, যেখানে একজন শিশু মানুষ হবে—মানবিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও সৃজনশীল। যেখানে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শুধু পেশা নয়, চরিত্র গঠন। অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, “শিক্ষা এমন হতে হবে যা মানুষকে কেবল চাকরি নয়, জীবনের অর্থ খুঁজে নিতে শেখায়। একজন শিক্ষার্থী যদি সঠিকভাবে শেখে চিন্তা করতে, সহযোগিতা করতে ও ভালোবাসতে—তবে সে যেখানেই থাকুক, সমাজকে আলোকিত করবে।” এই কথাগুলো যেন পুরো শিক্ষাজগতের জন্য এক নৈতিক দিকনির্দেশনা।

আজ আমাদের শিশুদের চোখে আনন্দের আলো নেই; তাদের কাঁধে বইয়ের বোঝা, মনের ভেতর অজানা ভয়। অথচ তারা তো ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। তাদের মুখে যদি হাসি না থাকে, তাদের মন যদি মুক্ত না হয়, তবে আমরা কেমন দেশ গড়ব? তাই এখনই সময়—শিক্ষাকে মুক্ত করার, শেখাকে আনন্দময় করার, জ্ঞানকে মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত করার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি সত্যিই মানুষ তৈরি করতে পারে, তবেই একদিন আমরা গর্ব করে বলতে পারব,“হ্যাঁ, এই দেশ আলোর পথে হাঁটছে।”
লেখক পরিচিতি : জুবাইয়া বিন্তে কবির
প্রশিক্ষক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বরিশাল।



 ডেস্ক রিপোর্ট
ডেস্ক রিপোর্ট